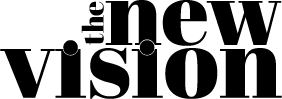স্ট্রোক মূলত তিন প্রকার। যেমন ইস্কেমিক স্ট্রোক (মাথার রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যে স্ট্রোক হয়), হেমোরেজিক স্ট্রোক (রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে যে স্ট্রোক হয়), ট্রান্সিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক (অনির্দিষ্ট কোনো কারণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে যা হয়)।
এর মধ্যে মস্তিষ্কের ভেতরের রক্তনালি বন্ধ হয়ে কিংবা ছিঁড়ে গিয়ে যে স্ট্রোক হয়, তার প্রভাব কতটা দীর্ঘমেয়াদি হবে বা স্বল্পমেয়াদি হবে, তা নির্ভর করে মাথার ঠিক কোনো অংশে স্ট্রোকটা হয়েছে এবং স্ট্রোক–পরবর্তী কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
যেহেতু স্ট্রোকের ধরন, মস্তিষ্কের অংশের ওপর নির্ভর করে রোগীর ওপর প্রভাব পড়ে, তাই স্ট্রোক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকদের পক্ষেও সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয় না যে ঠিক কত দিনে রোগী আগের মতো জীবন যাপন করতে পারবেন বা আদৌ পারবেন কি না।
তবে মস্তিষ্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ আছে যেগুলো আমাদের হাঁটাচলা, হাত–পা নাড়ানো, কথা বলা, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, বুঝতে পারা, চোখে ঠিকমতো দেখা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। স্ট্রোকের ফলে ওই সব অংশ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেসব অংশের নির্দিষ্ট কাজ প্রভাবিত হবে।
যেগুলো পরে নিউরোলজিস্ট কর্তৃক প্রদেয় নিয়মিত ওষুধ এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট থেরাপির মাধ্যমে উন্নতি করা সম্ভব।
রক্তনালি ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে যে হেমোরেজিক স্ট্রোক হয়, তার প্রথম কারণই হচ্ছে ‘হাইপারটেনশন’ এবং ‘অনিয়মিত প্রেশারের ওষুধ’–এর প্রভাব। মস্তিষ্কের অংশ এবং আরও কয়েকটা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে রোগী অপারেশনের প্রয়োজন আছে কি না।
স্ট্রোকের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
- কগনিটিভ ডিসফাংশন যেমন স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলা, মনোযোগ ধরে রাখতে না পারা, সহজ কাজও করতে না পারা।
- কথা জড়িয়ে যাওয়া, কথার গতি হারিয়ে যাওয়া, কথার মধ্যে কোনো মিল বা কথার কোনো অর্থ না থাকা
- বিষণ্নতা, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা এবং পোস্ট ট্রমাটিক ডিসট্রেস।
ওষুধের সঙ্গে আরও যা যা প্রয়োজন
- ফিজিওথেরাপি
- স্পিচ থেরাপি
- অকুপেশনাল থেরাপি
- সাইকো থেরাপি
স্ট্রোক–পরবর্তী উন্নতিগুলো সাধারণত খুবই ধীরগতিতে হয়, তাই কোনোভাবেই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে, এমন ভাবনার প্রয়োজন নেই। সেই সঙ্গে রোগীকে সর্বোচ্চ মানসিক সাপোর্ট দেওয়াটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
ডা. হিমেল বিশ্বাস, ক্লিনিক্যাল স্টাফ, নিউরোলজি বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা।